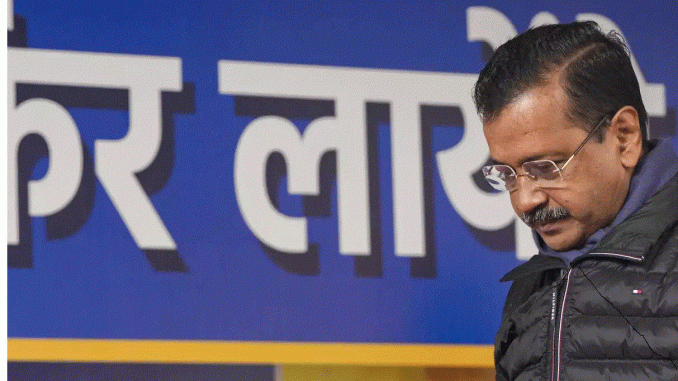
অভিজিৎ কুণ্ডু

শেষমেশ যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াইয়ের যে প্রাথমিক শর্ত ও এজেন্ডা নিয়ে তৈরি হয়েছিল আপ,সেই দুর্নীতির অভিযোগই আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল এই নতুন রাজনৈতিক উদ্যোগকে।
ভারতবর্ষে নির্বাচনী বিশ্লেষণে সংখ্যাভিত্তিক অভিজ্ঞতায় আটকে থাকলে হতাশা থেকে উল্লাস পর্যন্ত বিস্তৃত যে রাজনৈতিক বর্ণালী – সেটাকে ঠিকঠাক ধরতে পারব না। দিল্লি বিধানসভা ভোটে আম- আদমি পার্টির হেরে যাওয়া আর সাম্প্রতিক অতীতে বারবার নাস্তানাবুদ হয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির শেষমেশ দিল্লি বিধানসভা দখলএ করে নেওয়ায় কী কী প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেল? দিল্লির ভোটার সমাজ কোনও দিশা কি দেখাতে পারল?
সবচেয়ে জনপ্রিয় বয়ান হল – আপ দুর্নীতির পাঁকেই আটকে গেল। বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে আজ এই হাল হয়েছে আম আদমি পার্টির। পাশাপাশি রয়েছে ভোট-কাটাকুটি ভিত্তিক ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যায় কংগ্রেসের দিকে তীর ছুঁড়ে দিচ্ছেন সবাই। কেউ কেউ বলছেন আদতে বিজেপির বি-টিমকে জিইয়ে রেখে কী লাভ? সফট হিন্দুত্ববাদী আপ-এর মতো দলগুলোকে বাদ দিয়ে সরাসরি এ-টিমের অধীনস্থ হওয়া যাক। আর সবচেয়ে চমকপ্রদ প্রতিক্রিয়া হল – মোদির কেন্দ্রীয় সরকার বারবার আপ-এর কাছে দিল্লি বিধানসভা ভোটে পরাজিত হয়ে আপ-কে কাজ করতে দেয়নি। যতটুকু সীমিত ক্ষমতা দিল্লি রাজ্য হিসেবে পায়, তাতেও কলকাঠি নেড়েছে কেন্দ্র। ভোটার সমাজ বুঝে নিয়েছে আপ-কে আবার ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনলে একই ফল হবে, কেন্দ্র আবার কাজ করতে দেবে না। তাই আকচা-আকচি রেখে কেন্দ্রে ও রাজ্যে একই সরকার হোক, তাতেই জনহিত।
তাহলে নয়া শতাব্দীর নয়া প্রতিশ্রুতির কী হবে? এক দশক কাটতে না কাটতেই মুখ থুবড়ে পড়ল সিভিল সোসাইটি জারিত ভলান্টিয়ার-চালিত নয়া রাজনীতির প্রতিশ্রুতি। প্রচলিত সংসদীয় দলগুলির ওপর ভরসা কমে আসার প্রেক্ষিতেই নাগরিক সমাজ থেকেই জন্ম নিয়েছিল আপ-এর মতো নবীন রাজনৈতিক দল। মূলত রাজধানী-ভিত্তিক শক্তি হলেও আপ একটু একটু করে শাখা ছড়িয়েছে বেশ কিছু রাজ্যে। পঞ্জাবে রাজ্য সরকারও গঠন করে ফেলেছে আপ। তবুও দিল্লির সাম্প্রতিক হার যেন জল ঢেলে দিয়েছে আপ-এর উত্থান প্রকল্পে। ‘কেন্দ্র’ থেকে বিকীর্ণ হওয়া রাজনীতি যদি সেই ‘কেন্দ্রেই’ হেরে বসে, তাহলে স্বাভাবিক কারণেই দমে আসবে সেই বিকীরণ!
IAC, ‘ইন্ডিয়া এগেইনস্ট করাপশন’ গত দশকের গোড়ায় উত্তাল করে তুলেছিল দেশের রাজধানীকে। সেই বার্তা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল নয়া মিডিয়ার নিত্যনতুন অভিনব প্রচার কৌশলে। ভারতবর্ষের বুকে যেন নেমে এসেছিল এক ‘নয়া দৌড়’। তাবড় সমাজকর্মী, আইনজীবী, গবেষক, সাংবাদিক জড়ো হয়েছিলেন দিল্লির রামলীলা ময়দানে। ভারতবর্ষের বুকে রাজনীতির নতুন দিশা দেখানো জয়প্রকাশ নারায়ণের পর এই প্রথম আরেক অনন্য প্রয়াস। তফাত হল, সাবেক রাজনীতির খোলনলচে থেকে বেরিয়ে অনেকটা NGO স্টাইলে রাজনৈতিক দল গড়ে তোলার চেষ্টা। আপ হল সেই ‘ইন্ডিয়া এগেইনস্ট করাপশন’-উপজাত এক নতুন দিশা। প্রবীন সমাজকর্মী আন্না হাজারের ‘অরাজনৈতিক’ জন-আন্দোলনে নড়ে চড়ে বসেছিল নাগরিক সমাজ। ‘উর্জা’ অর্থাৎ এনার্জি, আবেগভরা নয়া উৎসাহের ডাক। একঘেয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর শ্লোগানের থেকে একটা স্বতন্ত্র বয়ানে আমরা অর্থাৎ পর্যবেক্ষকরাও চমৎকৃত হয়েছিলাম।
দুর্নীতি-বিরোধিতাকে সামনে রেখে নাগরিক সমাজের এগিয়ে থাকে একটা অংশ নয়া রাজনীতির বয়ান তৈরি করতে চাইল। দৈনন্দিন সমস্যা সমাধান বা সমাজ-সংস্কারের লক্ষ্যে এই রাজনীতি তত্ত্বগতভাবে ভরসা করে প্রযুক্তিগত যুক্তিশাসনের উপর। গোটা বিশ্বেই এই New Age রাজনীতি এখন লোকাল ও গ্লোবাল – পরস্পর সংযুক্ত এক পথের সন্ধান দিতে চায়। মানবাধিকারের প্রশ্নে এরা রাষ্ট্র মুখাপেক্ষী হতে চায় না। অগ্রাধিকার পাওয়ার কথা NGO এসোসিয়েশনদের যারা ট্রান্স ন্যাশনাল গ্লোবাল সোসাইটির কথা বলবে। জনহিত প্রধানত নির্ভর করবে রাষ্ট্র বিযুক্ত সামাজিক্ প্রকৌশলে। স্থানীয় আর বিশ্বায়িত সমাজের পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়ার মডেল-এ চলবে নতুন সমাজ গঠন। নেশন-স্টেট বা জাতিরাষ্ট্রের ভূমিকা এখানে ন্যূনতম।
বস্তাপচা রাজনীতি দেখতে দেখতে ক্লান্ত আমরা অনেকেই ভেবেছিলাম দিল্লির আপ বুঝি বা এক নতুন দিগন্ত খুলে দিতে চলেছে। নতুন শতাব্দীর আবির্ভাবের পরপরই আপ-এর উত্থান, বিকল্প জন-আন্দোলনের ভেতর থেকে। সেই আন্দোলনে পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদদের প্রাধান্য ছিল না। তাই, জনপ্রিয় ধারণায় কোনও ভুল ছিল না। নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় এসে জনস্বাস্থ্য ও জনশিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ও সদর্থক ভূমিকা পালন করেছে আপ। জন-পরিবহন ও জন-বণ্টনে জনতাকে নানা ‘সুবিধা’ পাইয়ে দিয়ে রাজ্যস্তরের নির্বাচনে পর পর সফল হয়েছে আপ। কিন্তু ভেতরে ভেতর কোনও এক সময় শুরু হয়েছিল রক্তক্ষরণ। অগ্রণী, শিক্ষিত, আলোকিত নাগরিক মুখ সম্বলিত দলের সমষ্টিবাচক চেহারা ক্রমে বদলে যেতে লাগল। ‘অরাজনৈতিক’, প্রাজ্ঞ, সচেতন যে মুখপাত্ররা এককালে আপ-কে জনসমাজে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল, তাঁরাই এক এক করে সরে যেতে লাগল। মূলস্ত্রোতের মার্কামারা আরও একটি রাজনৈতিক দলের মতোই কেন্দ্রীভূম কাঠামোর দিকে এগিয়ে গেল আপ।
কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকেন্দ্র ও তার চারপাশের নিকট বৃত্ত ঘিরেই দল পরিচালিত হতে থাকল। শেষমেশ যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াইয়ের যে প্রাথমিক শর্ত ও এজেন্ডা নিয়ে তৈরি হয়েছিল আপ,সেই দুর্নীতির অভিযোগই আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল এই নতুন রাজনৈতিক উদ্যোগকে। ‘গুড গভর্নেন্স’-এর শুভ দিকগুলো ক্রমশ পেছনে চলে গেল, সরে গেল নিম্নবর্গ বা পিছিয়ে থাকা শ্রেণির ভোটার সমাজের চাওয়া-পাওয়ার তত্ত্ব।
দিন-আনা দিন-খাওয়া মানুষগুলো তাঁদের প্রাত্যহিক যাপনের মসৃণতার খোঁজে নির্ভর করে এক-একটা রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক করিতকর্মা নেতাদের উপর, যারা দাঁড়িয়ে আছে রাষ্ট্র ও তাঁদের মাঝখানে, অনেকটা দালালের মতো। উচ্চশ্রেণি প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা ও সাহায্য নিতে যতটা সক্ষম, নিম্নবর্গ এ কাজে ততটাই অক্ষম। আর সংখ্যাগুরু এই সুবিধাহীন আম-জনতাই হল সাবেক রাজনীতির খদ্দের, পৃষ্ঠপোষক ব্যবস্থার যজমান। আমরা যে নয়া রাজনীতির প্রস্তাবনায় উল্লসিত হয়েছিলাম, যেসব আদর্শ সংকেতগুলো চিহ্নিত করেছিলাম, সে সবকিছু থেকে ধীরে ধীরে পিছিয়ে এসে ভারতীয় গণতন্ত্রের মূল স্রোতেই মিশে গেল এবং ভেসে গেল আপ।
অবশ্যম্ভাবী এই ভেসে যাওয়া। সমাজতাত্ত্বিক জন হ্যারিস তাঁর ‘পলিটিক্স ইজ আ ডার্টি রিভার’ প্রবন্ধে সমীক্ষা পেশ করেছেন তিন মেট্রোপলিটন শহরের – নয়া দিল্লি, সাও পাওলো এবং মেক্সিকো সিটি-র। তিন মহানগরীর তুলনামূলক গবেষণায় হ্যারিস বলছেন যে, নয়া রাজনীতি সফল হতে পারে শুধুমাত্র সেইসব সমাজে, যেখানে গণতন্ত্র উদার সমাজকে আরও বিকশিত করে তুলেছে। স্বাধীন বাজারের সাথে সাথে উদার জনজীবন লিবারাল ডেমোক্রেসি বা উদার গণতন্ত্রের প্রাথমিক শর্ত। NGO-র সক্রিয়তা যে সঙ্গ-অনুষঙ্গের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে লিবারাল ডেমোক্রেসিতে, তার চেয়ে শত হস্ত দূরে ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবা মূলক কার্যকরী কাঠামো ও তার শ্রেণিচরিত্র। তুলনায় প্রচলিত রাজনৈতিক দলগুলি অনেক বেশি কার্যকরী আম জনতার দরবারে। যে সমাজে সিটিজেন বা নাগরিক সত্তার থেকে ডেনিজেন বা পরভূক সত্তা বেশি গ্রাহ্য, সেখানে নয়া রাজনীতির বিকাশের সম্ভাবনা আরও সীমিত। তাই গাড্ডায় ভেসে যায় আপ, হাম আউর সব।

